The Rise of English Bangla
Basic Information:
- Writer: Terry Eagleton (1943-present).
- Book: Literary theory. An Introduction. The Rise of English is the 2nd chapter of the Book.
- Published date: 1983.
- Genre: Essay.
Topic of Discussion: English in the 18th century onward.
Ages of Discussion: Neoclassical, Romantic, Victorian and Modern.
Theme: The development of English literature and langu age.
Background of the Essay: ঈগলটন বলেছেন কিভাবে লিটারেচার বর্তমান যুগে এসেছে। আর ধর্মের উপরে কিভাবে লিটারেচার প্রাধান্য পেয়েছিল। পাশাপাশি কীভাবে ইংরেজি ভাষা এবং কালচার পৃথিবী জুড়ে ছড়িয়ে পড়েছে। মধ্য ভিক্টোরিয়ান যুগের দিকে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উন্নয়নের কারণে ধর্মের প্রতি মানুষের আস্থা হারিয়ে যাচ্ছিল। মানুষ ধর্ম থেকে দূরে সরে যাচ্ছিল। আর সেই সময়ে ধর্মের জায়গাটা লিটারেচার নিয়ে নিয়েছিল। আর এই বিষয়টা নিয়েই টেরি ঈগলটন এই প্রবন্ধে আলোচনা করেছেন।
বাংলা সামারি
তো সম্পূর্ণ বাংলা সামারি আমরা মাত্র ৬টা পয়েন্টের মাধ্যমে খুব সহজেই জানতে পারবো।
১. অষ্টাদশ শতকের ইংল্যান্ডের সাহিত্য সম্পর্কে ধারণা
২. সপ্তদশ শতাব্দীর সাহিত্য
৩. অষ্টাদশ শতাব্দীর লিটারেচারের কালচার
৪. রোমান্টিক পিরিয়ড
৫. ভিক্টোরিয়ান পিরিয়ড
৬. সাহিত্য কিভাবে পাঠ্য সিলেবাসের অন্তর্ভুক্ত হয়?
তো চলুন এবার এই পয়েন্ট গুলো আলোচনা করা যাক।
অষ্টাদশ শতকের ইংল্যান্ডের সাহিত্য সম্পর্কে ধারণা:
লিটারেচার এর বিষয়বস্তু: অষ্টাদশ শতাব্দীর লিটারেচার খুব একটা ক্রিয়েটিভ এবং ইমাজিনেটিভ ছিল না। কারণ শুধুমাত্র এই দুইটা গুণ দিয়ে কোন লিটারেচার লিখা হতো না। এর পাশাপাশি সমাজ, ইতিহাস, ঐতিহ্য, সামাজিক মূল্যবোধ ও রাজনীতি সবকিছুই লিটারেচার এর অন্তর্ভুক্ত ছিল। তখনকার সময়ে যে কোন লেটার, কবিতা ও ইতিহাস লিটারেচার এর অন্তর্ভুক্ত ছিল।
আপার ক্লাস মানুষদের মনোরঞ্জন: তবে এটা ছিল মূলত আপার ক্লাস মানুষদের মনোরঞ্জনের জন্য। অর্থাৎ তাদের যদি মনোরঞ্জন, টেস্ট ও ভ্যালু অন্তর্ভুক্ত করা না হয়, তাহলে সেই কাজটা লিটারেচার এর অন্তর্ভুক্ত হতো না। আর এটাকে বলা হতো পোলাইট লেটারস। অর্থাৎ এর দ্বারা বোঝা যাচ্ছে, অষ্টাদশ শতাব্দী লিটারেচার মূলত আপার ক্লাস মানুষদের জন্যই লিখা হতো।
ইংলিশ নোভেলের উৎপত্তি এবং বিকাশ: অষ্টাদশ শতাব্দীতেই ইংলিশ নোভেলের উৎপত্তি এবং বিকাশ ঘটে। তবে এটা লিটারেচার এর অন্তর্ভুক্ত হবে কিনা এর জন্য আপার ক্লাস মানুষেরা একটা রায় দেন। তাদের মতে, নোভেল অবশ্যই লিটারেচার এর অন্তর্ভুক্ত হবে, তবে নোবেলে অবশ্যই আপার ক্লাস মানুষদের মনোরঞ্জন করতে হবে এবং তাদেরকে গ্লোরিফাই করতে হবে।
সপ্তদশ শতাব্দীর সাহিত্য: সপ্তদশ শতাব্দীতে ইংল্যান্ডে গৃহযুদ্ধ হয়। তাই সমাজ বস্তা ভেঙে পড়ে এবং মানুষ একাকী হয়ে পড়ে। এই যুগকে বলা হতো নিউ ক্লাসিক্যাল পিরিয়ড। এই পিরিয়ডের কবিরা রিজন, নেচার, ও অর্ডার নিয়ে লিখতো। আর তাই মানুষজন লিটারেচার এর মধ্যে নিজের আত্মার সন্তুষ্টি খুঁজে পেতে শুরু করে। আর ধর্ম থেকে দূরে সরে যেতে থাকে। আর এই যুগের লেখকরা আপার ক্লাস এবং মিডিল ক্লাস উভয় ক্লাসকেই সন্তুষ্ট করতে পারছিল, নিজেদের লেখনীর দ্বারা। ভেঙে পড়া সমাজ ব্যবস্থাকে তারা পুনরায় তাদের লেখনীর দ্বারা গড়ে তোলে। আর আপার ক্লাস এবং মিডিল ক্লাসের মধ্যে যে গ্যাপ ছিল, এইটা তারা দূর করতে সফল হয়।
আরও পড়ুন: Bangla summary The Metaphysical Poets
অষ্টাদশ শতাব্দীর লিটারেচারের কালচার: আগের যুগ গুলোতে লিটারেচার ছিল মূলত মৌখিক। কিন্তু অষ্টাদশ শতাব্দীতে এসে লিটারেচার লিখিত আকারে পাবলিস্ট হতে শুরু করে। তখনকার লিটারেচারকে বলা হতো কফি হাউজ কালচার। অর্থাৎ মানুষজন কফি হাউসে বসে বিভিন্ন সোশ্যাল বিষয় নিয়ে আলোচনা করতো। আর এই সবকিছুই লিটারেচার এর আলোচনার বিষয়বস্তু হয়ে ওঠে। যা কিনা তৎকালীন লেখকরা খুব সুন্দর করে অবজার্ভ করতেন এবং তাদের লেখনীতে তুলে ধরতেন।
রোমান্টিক পিরিয়ড: রোমান্টিক পিরিয়ডে এসে ক্রিয়েটিভ এবং ইমাজিনেটিভ রাইটিংগুলোই লিটারেচার হয়ে ওঠে। এই সময়টায় Prose এবং Essay এর প্রভাব কমতে শুরু করে। আর রোমান্টিক পিডিয়ডের কবিতার প্রতি মানুষের আগ্রহ সৃষ্টি হয়। এর পেছনে একটা কারণ ছিল। মানুষ মূলত দুঃখ-দুর্দশার মধ্য দিয়ে সময় পার করছিল।
আর এই রোমান্টিক যুগের কবিতাগুলো ছিল মূলত কল্পনাভিত্তিক। তাই মানুষজন নিজেদের দুঃখ কষ্ট ভুলতে কল্পনার জগতে হারিয়ে যেত। রোমান্টিক যুগের শুরুটাই হয়েছিল French revolution এর পরেই। এই রেভুলেশনে অনেক মানুষ মারা যায় এবং মানুষের জীবন দুর্বিষহ হয়ে ওঠে। কিন্তু রোমান্টিক কবিদের কবিতায় মানুষজন টেম্পোরারি একটা প্রশান্তি পেত।
আবার রোমান্টিক কবিরা সেই সময় রাজনীতি, সামাজিক বিভিন্ন বিষয় ও সামাজিক মূল্যবোধ সবকিছুই কল্পনার মধ্যে দিয়েই সুন্দরভাবে উপস্থাপন করতো। অর্থাৎ এই সময়টা তারা সিম্বল ব্যবহার করে পলিটিক্যাল বিভিন্ন বিষয় উপস্থাপন করতো। যেহেতু রোমান্টিক যুগের অনেক কবি সরাসরি রাজনীতির সাথে জড়িত ছিল, তাই তারা রাজনীতিকে কবিতার সাথে খুব সুন্দর করে মিলিয়ে উপস্থাপন করতে পারতো।
আর তাই এই কবিতাগুলো অনেক বেশি জনপ্রিয় হয়ে উঠে থাকে। আবার দুঃখ কষ্ট ভুলতে মানুষ প্রকৃতির আশ্রয় নিয়েছে। যেমন, William Wordsworth দুঃখ কষ্ট ভোলার জন্য প্রকৃতিকে আশ্রয় করেছেন, William Blake তার কবিতায় রাজনৈতিক এবং (Song of Innocence and of Experience) মনস্তাত্ত্বিক অনেক বিষয় তুলে ধরেছেন।
John Keats পার্থিব জীবন সম্পর্কে শিক্ষা দিয়েছেন। P.B. Shelley তার কবিতা Ode to West wind এ পরিবর্তনের ডাক দিয়েছেন। এভাবেই কল্পনা এবং বাস্তবতার একটা সংমিশ্রণ ঘটিয়ে মানুষের হৃদয়ে প্রশান্তি দিতেন রোমান্টিক পোয়েটরা। এসব কারণেই রোমান্টিক পোয়েটরা ইংলিশ লিটারেচারকে উপরে তুলতে অনেক ভূমিকা পালন করেছিলেন। আর তাই এই যুগের কবিতা Aesthetic বা নান্দনিক যাত্রা শুরু করে।
Symbol:
সিম্বল সম্পর্কে বলতে গিয়ে ঈগলটন বলেন, সিম্বলের মাধ্যমে লেখকরা সমাজের অনেক বিষয় তুলে ধরেছেন। আর এটা রোমান্টিক কবিরাই সর্বপ্রথম শুরু করেন। রোমান্টিক যুগ থেকে মূলত কবিতা অনেক বেশি জনপ্রিয় হতে শুরু করে। আর তাই যখনি কবিতার সমালোচনা করা হয়েছে, কেউ না কেউ কবিতাকে সমর্থন করে ক্রিটিসিজমের হাত থেকে রক্ষা করেছেন এবং কবিতাকে উপরে টেনে তুলেছেন। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে, Sir Philip Sidney এর “An Apology for Poetry” এবং Shelley এর “The Defence of Poetry”.
ভিক্টোরিয়ান পিরিয়ড: এরপরে চলে আসে ভিক্টোরিয়ান পিরিয়ড। এখানে নতুন নতুন সাইন্টিফিক ইনভেনশন হয়। আর তাই মানুষ ধর্মের প্রতি আস্থা হারিয়ে ফেলে। মানুষ বুঝতে পারছিলো না যে, ধর্মকে বিশ্বাস করবে নাকি বিজ্ঞানকে? কারণ ধর্ম এবং বিজ্ঞানের অনেক বিষয়ে মিল হচ্ছিল না বা বিপরীতমুখী ছিল। বিজ্ঞান ধর্মের বিভিন্ন বিষয়কে প্রশ্নবিদ্ধ করতে থাকে। এজন্যই ধর্মের পূর্বের বিশ্বাসগুলো ভেঙে যেতে শুরু করে। আর বিজ্ঞানের প্রতি ঝুঁকে পড়ে। এই জায়গাটায় ধর্মীয় বিশ্বাস থেকে দূরে সরে আসার কারণে মানুষ আত্মিকভাবে দেউলিয়া হয়ে পড়ে অর্থাৎ মানুষ হৃদয়ের প্রশান্তি পাচ্ছিল না। ধর্মের এই জায়গাটাই নিয়ে নেয় লিটারেচার। অর্থাৎ মানুষ আগে ধর্মে বিশ্বাসী থাকায় মানসিকভাবে যে শান্তি পাচ্ছিল, তা এখন লিটারেচার থেকে পেতে শুরু করেছিল।
পাশাপাশি ধর্মীয় প্রচারক এবং শাসকরা আগে ধর্ম দিয়ে সব ব্যাখ্যা দিচ্ছিল। কিন্তু সাইন্টিফিক ডিসকভারির কারণে ধর্মের সাথে অনেক বিষয়ের সংঘাত লেগে যাওয়ায় তারা এসবের ব্যাখ্যা আর দিতে পারছিল না। সামাজিক বিভিন্ন সমস্যার সমাধান দিতে পারছিল না। চার্চ মানুষের উপরে ডমিনেট করছিল। মানুষকে ডমিনেট করতে শাসকরা ধর্মকে হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করছিল। কিন্তু ধর্ম সামাজিক বিভিন্ন সমস্যার সমাধান না দিতে পারায়, শাসকরা তাদের কর্তৃত্ব হারাতে শুরু করে। এই সকল সামাজিক সমস্যার সমাধান লিটারেচার দিতে শুরু করে। তখন শাসক শ্রেণীও আবার লিটারেচার ব্যবহার করতে শুরু করে। Matthew Arnold এজন্য সরাসরি লিটারেচারকে ধর্মের জায়গা দিয়েছেন।
Work of Scrutiny: এটা ছিল একটি তৈমাসিক সাহিত্য সমালোচনার জার্নাল। এর মূল কাজ ছিল তৎকালীন লিটারেচারের ভুল ত্রুটি তুলে ধরা। এরা সমালোচনা করতো কিন্তু এর সমাধান দিত না। অর্থাৎ লিটারেচারের ভুল খুঁজে বের করতো কিন্তু কোনটা সঠিক হবে বা কিভাবে লিখলে সঠিক হবে, তা এই জার্নাল তুলে ধরতো না। তবে এটা সাহিত্য সমালোচক হিসেবে খুব ভালো কাজ করেছে। আবার তৎকালীন সময়ের বিভিন্ন সমস্যাও স্ক্রুটিনি তুলে ধরতো। কিন্তু এর সমাধান দিত না। তাই ইগলটন স্ক্রুটিনি এর কাজ এবং এর উদ্দেশ্যকে ব্যর্থ প্রচেষ্টা হিসেবে উল্লেখ করেছেন।
সাহিত্য কিভাবে পাঠ্য সিলেবাসের অন্তর্ভুক্ত হয়?
For Women : এ সম্পর্কে ঈগলটন বলেন তৎকালীন সমাজের মেয়েরা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি নিয়ে পড়ালেখার সুযোগ পেত না। অর্থাৎ তাদেরকে সেই সুযোগটা দেওয়া হতো না। তাদেরকে শুধুমাত্র লিটারেচার পড়তে দেওয়া হতো। অর্থাৎ তাদেরকে একটু অবহেলার চোখে দেখা হতো। আর এভাবেই লিটারেচার আমাদের পাঠ্য বইয়ে অন্তর্ভুক্ত হয়।
Civil Service Examination: তৎকালীন সময়ে ব্রিটেন ছিল পৃথিবীর পরাশক্তি। বলা হতো ব্রিটিশ রাজত্বে সূর্যাস্ত যেত না। যেহেতু বিশ্বের বিভিন্ন দেশে তাদের কলনি ছিল, তাই যারা সিভিল সার্ভিসে যোগদান করতো, তাদেরকে লিটারেচার পড়ানো হতো। এর কারণ হচ্ছে, তারা যদি নিজের দেশের ইতিহাস, ঐতিহ্য এবং সাহিত্য না জানতে পারে, তাহলে তারা তাদের ইতিহাস, ঐতিহ্যের প্রভাব অন্য দেশে ফেলতে পারবে না। তাই তাদের সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় লিটারেচারকে বাধ্যতামূলকভাবে পড়ানো হতো। এতে করে অন্য দেশে গিয়ে তারা নিজেদের দেশের কালচার তুলে ধরতে পারতো। আর এভাবেই ইংরেজি সাহিত্য বিশ্বজুড়ে ছড়িয়ে পড়ে এবং ইংরেজি কালচার সম্পর্কে পৃথিবীর মানুষ জানতে পারে।
আরও পড়ুন : Bangla summary The Study of Poetry
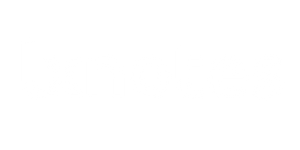

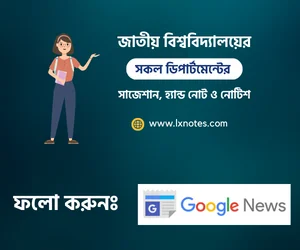
চমৎকার উপস্থাপনা।